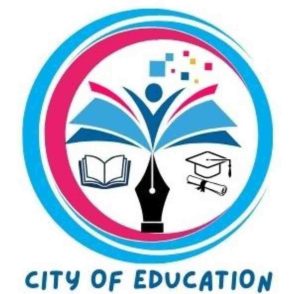বিষয়ের ধারণায়নঃস্বাস্থ্য সুরক্ষা (Wellbeing)
বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী বয়সভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং এর চ্যালেঞ্জ সঠিকভাবে মোকাবেলা করে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সুরক্ষিত থেকে নিজে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা। নিজের ও অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারবারিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক পরিসরে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সক্রিয় ও মানবিক নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা । বিষয়ের ধারণায় অন্তঃ ও আন্তঃব্যক্তিক পরিবর্তন এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নিজ স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সকলকে নিয়ে ভালো থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিজে ভালো থাকার এবং অন্যকে ভালো রাখার উপর মানুষের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ জীবন অনেকাংশে নির্ভর করে যা সুস্থ সমাজ এবং নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিপূর্বে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত যোগ্যতাসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ কিংবা সহ বা অতিরিক্ত শিক্ষাক্রমিক কাজ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। কিন্তু অন্তঃ ও আন্তঃব্যক্তিক পরিবর্তনের প্রভাব পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করে সকলকে নিয়ে ভালো থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকের কিছু বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এই যোগ্যতাসমূহ আপনা-আপনি তৈরি হয় না, বরং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষা ও পরিচর্যার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জিং, উপভোগ্য, সমসাময়িক, সক্রিয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা নিজের এবং অন্যের বৈশিষ্ট্য, সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা, আবেগ, অনুভূতি পছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণার ভিত্তিতে নিজেকে বুঝে এবং অন্যের অবস্থান অনুধাবন করে ইতিবাচক, কার্যকর যোগাযোগ ও সম্পর্ক ব্যবস্থাপনাসহ তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে নিয়ে সফল ও আনন্দময় জীবনযাপন করতে পারে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়টি ধারণায়নে প্রতিক্রিয়াভিত্তিক (Reactive) উদ্যোগের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতায়ন (Empowerment) কৌশল বিবেচনা করা হয়েছে যা সময়সাপেক্ষ হলেও শিক্ষার্থীদের কঠিন বাধা দূর করে ভিতর থেকে আত্মবিশ্বাসী ও মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে (Resilience) সহায়তা করে। এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজের ও অন্যের আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করে ভাব বিনিময় ও মত প্রকাশ, কার্যকর অংশগ্রহণ, আত্মবিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (বজায় রাখা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছিন্ন করা), সফলতা ও ব্যর্থতা অনুধাবন ও ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা, আবেগ ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা সর্বোপরি আত্ম-পরিচর্যার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ, সংবেদনশীল ও পরিশীলিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানুষ, সমাজ ও পৃথিবীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা অন্যের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ, বেদনা অনুধাবন করে সমব্যথা বা সম-আনন্দ অনুভব করে এবং সকল প্রকার ঝুঁকি, দ্বন্দ্ব, হতাশা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ নিরসনের মাধ্যমে মানব ও প্রকৃতি সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে অর্থবহ জীবনযাপনের মাধ্যমে ভালো থাকতে পারে । বিষয়ের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় নিম্নলিখিতভাবে এর ধারণায়ন করা হয়েছে। শরীর ও মনের যত্ন ও পরিচর্যা : স্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো নিজের পরিচর্যা অর্থাৎ নিজেকে ভালোবেসে শরীর ও মনের যত্ন ও পরিচর্যা করা। শিক্ষার্থীর শরীর, মন এবং পরিবেশের প্রতিনিয়ত অন্তঃ ও আন্তঃমিথ ক্রিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির স্বাস্থ্যকর, ইতিবাচক, সংবেদনশীল ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের যত্ন ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। সুতরাং নিরবিচ্ছিন্নভাবে আত্ম-পরিচর্যা করতে পারার যোগ্যতা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যক। দৈনন্দিন এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, রোগ ও দুর্ঘটনা, ঝুঁকি মোকাবেলা, আবেগ ব্যবস্থাপনা, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, চাপ মোকাবেলা, শখ ও বিনোদন, অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবা ইত্যাদি সার্বিকভাবে আত্ম-পরিচর্যার অংশ। আত্ম-পরিচর্যায় শরীর ও মনের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই নিজে ভালো থ াকার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে অন্যকেও ভালো রাখা । যথাযথভাবে জেনে, বুঝে, অনুধাবন ও উপলব্ধি করে কার্যকরী আত্ম-পরিচর্যা করতে হলে নিম্নবর্ণিত সক্ষমতাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ১. আবেগিক বুদ্ধিমত্তা : নিজের আবেগ অনুভূতির অনুধাবন ও উপলব্ধি, ইতিবাচকভাবে প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনাসহ অন্যের আবেগ ও অনুভূতি বোঝা এবং তা সম্মান করে যৌক্তিক ও স্বাস্থ্যকর যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা এবং ধৈর্য্য ও সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করার যোগ্যতা এই ধরণের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। চিন্তাকে যৌক্তিক, বিশ্লেষণধর্মী ও গঠনমূলক রেখে, প্রাধিকার নির্ধারণ করে ইতিবাচকভাবে ভূমিকা রাখতে পারাও এই যোগ্যতাসমূহের অংশ। ২. আত্ম-বিশ্লেষণ : নিজের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক মুল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ, মূল্যায়নকে বিশ্লেষণধর্মী ও গঠনমূলক রেখে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া, অনুভূতি ও আচরণের সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ সহায়তা চাইতে পারা ইত্যাদি এই ধরনের যোগ্যতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত । ৩. সামাজিক বুদ্ধিমত্তা : সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে সকলের সঙ্গে থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখা এবং নিজের কার্যক্রম ও ভূমিকায় সন্তুষ্ট থেকে নিজেকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসতে পারার জন্য সামাজিক বুদ্ধিমত্তা সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের এবং অন্যের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে যৌক্তিকভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক গঠন ও বজায় রাখা, আন্তঃ সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও চাপ মোকাবেলা/ব্যবস্থাপনা, ধৈর্য্য ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে আবেগ ও চাপমুক্ত থেকে দৃঢ়তা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও নমনীয়তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিরসন ও সমঝোতা করতে পারা এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক বজায় রাখতে পারা সামাজিক বুদ্ধিমত্তার অন্যতম যোগ্যতা । সুতরাং শরীর, মন, পরিবার ও সমাজের প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্লেষণ এবং সামাজিক বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে নিজেকে ভালোবেসে নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শরীর ও মনের যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালো থাকার এবং অন্যকে ভালো রাখার যোগ্যতা অর্জন করবে। ===000=== তথ্যসূত্র : শিক্ষাক্রম রুপরেখা-2021